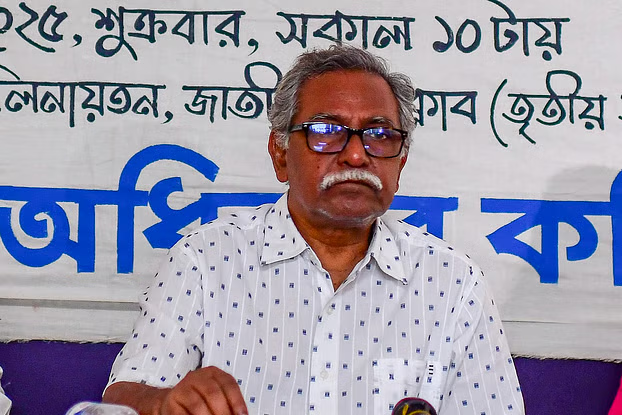বাংলাদেশ ব্যাংক কি পারে ব্যাংকিং খাতকে শুদ্ধ করতে?

বাংলাদেশ ব্যাংক পেয়েছে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, যার লক্ষ্য ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—এবারও কি কেবল ঘোষণা, নাকি সত্যিকারের পরিবর্তন? পড়ুন বিশ্লেষণ। ছবিঃ ডেইলি ষ্টার
নতুন ক্ষমতার পেছনের প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত অনেক বছর ধরেই একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। একদিকে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত ঋণ অনুমোদনের মতো সমস্যা খাতটির ভিত্তিকে নড়বড়ে করে তুলেছে। খেলাপি ঋণের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় এক লাখ কোটি টাকার কাছাকাছি, যা দেশের অর্থনীতির জন্য এক বড় ধরনের ঝুঁকি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ পর্যন্ত অনেকবার নানা নীতিমালা চালু করলেও বাস্তবায়নের অভাবে সেগুলো তেমন কাজে আসেনি। ফলে জনগণের আস্থা কমে গেছে, আর বিনিয়োগকারীরাও রয়েছেন দ্বিধার মধ্যে।
নতুন ক্ষমতা ও সম্ভাব্য পরিবর্তন
এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংককে কিছু নতুন ও কার্যকর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায়, সংস্থাটি এখন চাইলে দুর্বল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিতে পারবে, প্রয়োজনে এমডি বা সিইও’কে অপসারণ করতে পারবে এবং বড় ঋণের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন থেকে নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারবে এবং ব্যতিক্রমী বা সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনগুলোর ওপর নজরদারি বাড়াতে পারবে। এসব ক্ষমতা বাস্তব প্রয়োগে এলে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।
পুরনো অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান বাস্তবতা
যদিও ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, তবুও এ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—বাংলাদেশ ব্যাংক কি আসলেই স্বাধীনভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে? অতীতেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক একাধিকবার কিছু ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে তা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে, নতুন এই পদক্ষেপগুলো যেন রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে থেকে বাস্তবায়ন করা হয়, সে নিশ্চয়তা এখনো নেই।
জনআস্থা ও বিনিয়োগ সংকট
বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সাধারণ মানুষের আস্থা অনেকটাই কমে গেছে। বিভিন্ন ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারি, খেলাপি ঋণ, এবং গ্রাহকদের আমানতের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এখন সাধারণ। বহু মানুষ ব্যাংকিং লেনদেনের পরিবর্তে বিকল্প উপায় খুঁজে নিচ্ছেন, যেমন—মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা ব্যক্তিগত লেনদেন। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আরও দুর্বল হচ্ছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

ছবিঃ দ্যা বিসনেস স্টান্ডের
পরিচালন কাঠামো ও বোর্ড সদস্যদের জবাবদিহিতা
আরেকটি বড় সমস্যা হলো—ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা নয়, বরং রাজনৈতিক পরিচয়, আত্মীয়তা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভিত্তিতে সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়। এই বোর্ড সদস্যরা অনেক সময় ঋণ অনুমোদন বা পলিসি নির্ধারণে অব্যবস্থাপনা করেন, যার দায় পড়ে পুরো ব্যাংকের ওপর। বাংলাদেশ ব্যাংক যদি সত্যিকার অর্থে ব্যাংক রিফর্ম চায়, তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পরিচালন কাঠামোতে স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন জবাবদিহিতা
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে শুধুমাত্র নিয়ম বা আইন করলেই চলবে না, দরকার কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন এবং সবার জন্য সমান জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। একদিকে যদি একটি ব্যাংকের এমডি দুর্নীতির জন্য অপসারিত হন, অথচ অন্য ব্যাংকের কর্তা একই কাজ করেও রয়ে যান, তাহলে কোনো পরিবর্তনই টেকসই হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংককে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেখানে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় নয়, বরং তাদের কার্যক্রমই বিচার্য হবে।
ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা
বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে এখন একটি বড় সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ—ব্যবস্থা সংস্কার করে জনআস্থা ফেরানো এবং অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালিত করা। এই কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা দিতে হবে, এবং প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। একই সঙ্গে, ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ—সরকার, ব্যবসায়ী মহল, বিনিয়োগকারী, এবং সাধারণ জনগণ—সবার সমন্বয় ছাড়া এই খাতে টেকসই পরিবর্তন সম্ভব নয়। নতুন ক্ষমতা তখনই অর্থবহ হবে, যখন সেগুলো বাস্তবায়নের পেছনে থাকবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পেশাদার কর্মপ্রবাহ।